মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের ধারণা
এর ফলে রাতের আকাশের প্রতিটি বিন্দুতেই এত অগণিত সংখ্যক তারকা থাকতো যে সে আকাশ মধ্যাহ্ন সূর্যের চেয়েও ৪০ হাজার গুণ উজ্জল থাকতো। তাই প্রশ্ন শুধু এটা নয় যে রাতের আকাশ কেন কালো—প্রশ্ন এটাও যে দিনের আকাশও কেন এত “কালো” (অর্থাৎ যথেষ্ট উজ্জল নয়)। এর থেকে অলবার গাণিতিকভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে সমসত্ত্ব (Homogenous) এবং স্থির (Static) বিশ্বতত্ত্ব আমাদের পরিদৃশ্য স্বাভাবিক রাতের আকাশের সাথে খাপখায়না বলে তা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এর বিপরীতে যদি বিশ্বকে মনে করা যায় সসীম ও নির্দিষ্ট এলাকাভূক্ত (Finite edge) এবং তা ক্রমপ্রসারমান, তাহলেই রাতের আকাশের প্রকৃতি বর্তমানের মতো হওয়া সম্ভব।
এডুইন হাবলের মতবাদ
মহাবিশ্বের আয়তন সম্পর্কে ১৯২০ সন পর্যন্ত যে ধারণা বর্তমান ছিল তা আমাদের ছায়াপথ (Milky Way) এর পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তখন পর্যন্ত সমস্ত তারকারাজিকে মনে করা হতো এই ছায়াপথেরই অংশ। আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এড্যুইন হাবল ১৯২০ সনে প্রথম লক্ষ্য করেন যে, মহাকাশের অনেক দূরবর্তী তারকা আসলে তারকা নয়- এদের প্রত্যেকেই ছায়াপথের মতো এক একটি স্বতন্ত্র নীহারিকা। তার আরও গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী আবিস্কার হলো যে এইসব নীহারিকা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছ থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে- যা তাদের থেকে প্রাপ্ত আলোর বর্ণালী (Spectroscopy) বিশ্লেষণ করা বোঝা যায়।
এড্যুইন হাব্লই প্রথম আবিষ্কার করেন যে মহাবিশ্বের কোন পদার্থ যদি আমাদের কাছে সরে আসতে থাকে তবে তার আলোকরশ্মি বিশ্লেষণকালে নীল রঙের প্রান্তে (Blue spectrum) বিচ্যুত হবে এবং বিপরীত দিকে আমাদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকলে তা লাল রঙের প্রান্তে (Red spectrum) বিচ্যুত হবে। হাবূল পর্যবেক্ষণ করেন যে প্রায় সব দূরবর্তী নীহারিকাই আমাদের থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে। হাবল এ বিষয়ে একটি সূত্রও আবিস্কার করেন, যা হাবূলের সূত্র নামে পরিচিত- “নীহারিকার লোহিত বিচ্যুতির (Red shift) পরিমাণ তার দূরত্বের সাথে সমানুপাতিক।"
হাবূলের সূত্র প্রমাণ করে যে এই ক্রমপ্রসারণের কোন কেন্দ্রবিন্দু নেই- প্রত্যেকেই স্ফীতমান বেলুনের উপরিভাগে কালির ফোঁটার মত একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাশূণ্যে নীহারিকাগুলো দূরে সরে যাচ্ছে মনে হলেও অবশ্য আসলে তা নয়- স্বয়ং মহাশূন্য, যাতে নীহারিকাগুলো বর্তমান, তাই ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে।
এ জন্যেই যে কোন বিন্দু থেকে (যেমন আমাদের পৃথিবী) মনে হবে যে এটাই বিশ্বের কেন্দ্র এবং সমস্ত নীহারিকা আমাদের থেকে সমানভাবে সরে যাচ্ছে। তাই আমাদের থেকে সবচেয়ে দূরের বস্তুকে মনে হবে সবচেয়ে দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। হাবূলের আবিষ্কৃত এই সূত্র আইনষ্টাইন-ফ্রীডমানের মহাজাগতিক মডেলের সাথেও সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। হালের এই ক্রমপ্রসারমানতার তত্ত্বটি স্থির বিশ্বের (Isotropic, homogenous & static) পরিবর্তে ক্রমপ্রসারমান বিশ্বতত্ত্বের (Isotropic, homogenous & expanding) দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করে যা পূর্বোল্লিখিত অলবারের ধাঁধারও সমাধান দেয়।
আইনষ্টানের মহাজাগতিক মডেল (Cosmic Model)
১৯১৭ সনে জার্মান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইন প্রথমবারের মতো "মহাজাগতিক মডেল (Cosmic model)" তৈরী করার প্রয়াস নেন তার নিজের আবিষ্কৃত আপেক্ষিকতাবাদের সূত্র (Theory of Relativity) এবং স্থির বিশ্বতত্ত্বকে ভিত্তি করে (কারণ তখন পর্যন্ত হাবূল আবিষ্কার করেননি যে মহাবিশ্বের সমস্ত নীহারিকা ও বস্তুপুঞ্জ একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।) এর ফলশ্রুতিতে আইনষ্টাইন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে,
১) মহাবিশ্ব সীমাহীন বা অনন্ত হতে পারেনা এবং
২) মহাবিশ্ব সান্ত বা সসীম হয়ে সীমাহীন শূন্যস্থান দ্বারাও পরিবেষ্টিত হতে পারেনা।
তার এই দু'টি সিদ্ধান্ত ‘চিরায়ত স্থির মহাবিশ্ব ধারণা ব্যাখ্যা করার জটিলতাকে আরো ঘনীভূত করে তুলে।এর সমাধান হিসাবে আইনষ্টাইন যে প্রকল্প প্রণয়ন করেন তা হচ্ছে মহাশূন্যকে চিরন্তন ইউক্লিডীয় জ্যামিতি অনুসারে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কেননা তা দু'হাজার বছর পূর্বে মাটির পৃথিবীর ত্রৈমাত্রিক জগতের সঙ্গে সংগতি রেখে তৈরী করা হয়েছে মহাশূন্যের চতুর্মাত্রিক জগতের পরিপ্রেক্ষিতে তা সংগতিপূর্ণ নয়। আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব থেকে আইনষ্টাইন সিদ্ধান্তে আসেন যে, মহাজাগতিক মাত্রায় (Cosmic or Astronomical Dimension) মহাশূন্যের জ্যামিতি আসলে অ-ইউক্লিডীয়, যদিও পার্থিব মাত্রায় (Terrestrial Dimension) এই জ্যামিতির সাথে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির কোন দ্বন্দ্ব দেখা যায় না। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা যেমন একটি সীমা পর্যন্ত নিউটনীয় বলবিদ্যাকে কার্যতঃ অন্তর্ভূক্ত করে, অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতিও তেমনি একটি মাত্রা পর্যন্ত ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে কার্যতঃ অন্তর্ভূক্ত করে। ইউক্লিডের পরিবর্তে নতুন মহাজাগতিক জ্যামিতি অনুসারে আইনষ্টাইন সিদ্ধান্ত নেন যে পদার্থের উপস্থিতি স্থান- কালকে বাঁকা করে দেয়, তবে এই বক্রতাকে কেউ দেখতে পায় না। তার মতে আমরা চতুর্মাত্রিক মহাবিশ্বকে ত্রৈমাত্রিক রূপে দেখতে পাই।
পদার্থের উপস্থিতিই এখানে চতুর্থ মাত্রাটির জন্ম দেয়, যেভাবে পৃথিবীর দ্বিমাত্রিক অবতলে পাহাড়ের উপস্থিতি তৃতীয় একটি মাত্রার জন্ম দেয়। এই নুতন মহাজাগতিক জ্যামিতি অনুসারে আইনষ্টাইন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন যে মহাশূন্য সসীম এবং হয় তা পজিটিভ ভাবে বাঁকা, অর্থাৎ গোলকের মধ্যে আবদ্ধ- অথবা তা নেগেটিভ ভাবে বাঁকা। এর মধ্যে কোনটি সঠিক তা অবশ্য জানা যায়নি। আর আইনষ্টাইনের মহাবিশ্ব কখনও স্থির হতে পারেনা- হয় তা প্রসারমান (Expanding) অথবা সংকোচয়মান (Contracting): এ দুটোর মধ্যে একটা হতে হবে।
আইনষ্টাইন এই মহাজাগতিক মডেল প্রণয়ন করতে গিয়ে তিনি তার বৈজ্ঞানিক জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছিলেন মহাজাগতিক একক (Cosmological constant) ব্যবহার করে। পরে তিনি নিজে এই ভুল স্বীকার করে তাকে বাদ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই মহাজাগতিক মডেল সম্পূর্ণ হয় ১৯২২ সনে সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ আলেকজান্ডার ফ্রীডমানের গাণিতিক সমাধানের মাধ্যমে যা বর্তমান কাল পর্যন্ত মহাজগতের সঠিক গাণিতিক ব্যাখ্যা হিসাবে সমাদৃত হয়ে আছে। আইনষ্টাইন—ফ্রীডমান মডেল অনুসারে মহাজগত তার মধ্যে উপস্থিত বস্তুর ঘনত্বের উপর নির্ভর করে হয় আক্ষরিক অর্থে চির প্রসারমান (Everexpanding) হতে থাকবে; অথবা প্রসারমান মহাবিশ্ব কোন একদিন প্রসারণ বন্ধ করে আবার উল্টোদিকে সংকুচিত (Collapsing) হতে থাকবে।
এর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনটি সত্য তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি, কেননা মহাবিশ্বে মোট বস্তুর পরিমাণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে এখনও মাপা সম্ভব হয়নি বলে। যদি এই বস্তুর বাস্তবিক ঘনত্ব সংকোচনের জন্য প্রয়োজনীয় ঘনত্বের (Critical density of matter) 4 যা গাণিতিক ভাবে দাঁড়ায় প্রতিঘন সেন্টিমিটারে ১০-৩০ গ্রাম বস্তু) চেয়ে কম হয় তবে মহাবিশ্ব অনন্তকাল শুধু প্রসারিত হয়ে যেতে থাকবে।
আর যদি বাস্তবিক ঘনত্ব এই প্রয়োজনীয় ঘনত্বের চেয়ে বেশী হয়, তবে বর্তমানে প্রসারমান এই মহাবিশ্ব কোন একদিন তার মহাকর্ষ বলের প্রভাবে আবার সংকুচিত হতে শুরু করবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পরে আবার তার শুরুর স্থানটির মতো একটি বিন্দুতে এসে উপস্থিত হবে। মহাবিশ্বের শুরুর মুহূর্তে একক বিন্দুটিকে যেমন বলা হয় Big Bang তেমনি তার এই শেষ মুহূর্তের একক বিন্দুটিকে বলা হয় Big Crunch ।
মহাবিশ্বের প্রসারমান নীহারিকাপুঞ্জ
আমরা আমাদের মহাবিশ্ব সংক্রান্ত আধুনিক ধারণাকে সরলীকৃত করতে পারি এভাবে যে আমাদের ছায়াপথ তার ১০ হাজার কোটি তারকাসম্বলিত এবং ১ লাখ আলোকবর্ষ পরিমাণ পরিধির বিশালতা সত্ত্বেও তা মহাবিশ্বের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। এরকম ‘ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র” আরো নীহারিকা যাদের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার কোটি এবং এর কোনটি ছায়াপথ থেকে বড় এবং কোনটি ছোট– এ সমস্ত নিয়েই আমাদের মহাবিশ্ব গঠিত। এ হিসাবে মহাবিশ্বের মোট তারকার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দশ কোটি কোটি কোটি (১০২২)। নীহারিকাগুলো আবার কিছু কিছু গুচ্ছের আকারে একত্রিত কয়েকটি থেকে কয়েক হাজার পর্যন্ত নীহারিকা নিয়ে এক একটি গুচ্ছ (Cluster)। আমাদের ছায়াপথ যে নীহারিকা গুচ্ছের অন্তর্ভূক্ত, তাতে রয়েছে ৩০ টিরও বেশী নীহারিকা এবং এই নীহারিকাগুচ্ছটির ব্যাস ৬৫ লক্ষ আলোকবছর। এসমস্ত নীহারিকাগুচ্ছ ক্রমাগত একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সেই সাথে স্থান-কালের মাত্রাকে প্রসারিত (Stretching) করে মহাবিশ্বের ‘সীমানা' ক্রমপ্রসারমান।
এ ধারণা থেকেই অনিবার্যভাবে বেরিয়ে আসে যে প্রসারমান মহাবিশ্ব অতীতে আরও ছোট ছিল— অর্থাৎ যতোই সময়ের অতীত পানে যাওয়া যাবে ততোই তার আকারও ছোট হয়ে আসবে। এ ভাবে পিছনে যেতে যেতে দেখা যাবে যে কোন একসময়ে তার সমস্ত বস্তু, অর্থাৎ বর্তমান নীহারিকাগুচ্ছ, তারকারাজি, গ্যাসপুঞ্জ, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ একটা নির্দিষ্ট একক সত্ত্বায় (Singularity) ঘনীভূত ছিল।
এখানেই প্রশ্ন উঠে যে বর্তমানে দৃশ্য মহাবিশ্ব কি চিরকাল ধরে অস্তিত্বমান ছিল, নাকি 'কোন এক সময়ে’ তার সৃষ্টি হয়েছে? আইনষ্টাইন-ফ্রীডমান মডেলও আমাদের গাণিতিকভাবে প্রমাণ করে যে মহাবিশ্ব তার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে এক অদ্বিতীয় গাণিতিক একক বিন্দু (Mathemetical singularity) থেকে উদ্ভূত হয়ে যার থেকে উৎপত্তি স্থান/কালের এবং বস্তু/শক্তির। মহাবিশ্বের এই উৎসমূহুর্তটিই আখ্যায়িত বিগ ব্যাংগ নামে।
মহাশক্তির ধারণা
সূচনালগ্নের মহাবিস্ফোরণের ফলে ক্রমপ্রসারমান এই মহাবিশ্বের ধারণার বাস্তব কোন প্রমাণ অবশ্যই বিজ্ঞানীদের পেতে হয়েছে; খুঁজে পেতে হয়েছে এমন কোন 'ফসিল' যা এই ধারণাকে বাস্তব বলে প্রমাণ করবে। দীর্ঘদিন যাবত অনেক বিজ্ঞানীই ধারণা পোষণ করতেন যে এই মহাবিস্ফোরণের কোন না কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া উচিত। বিগব্যাংগের মাধ্যমে মহাবিশ্বের উৎপত্তি তত্ত্বের একজন বড় সমর্থক ও ব্যাখ্যাকারী জর্জ গ্যামো ১৯৫০ সনের দিকে অভিমত প্রকাশ করেন যে মহাবিস্ফোরণ থেকে ছড়িয়ে পড়া উত্তাপের কিছু না কিছু অবশেষ এখনও মহাবিশ্বে অস্তিত্বমান রয়েছে, যদিও দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাকে কেউ প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করতে পারেন নি।১৯৬৪ সনে দু’জন বৈজ্ঞানিক, আনো পেনজিয়াস এবং রবার্ট উইলসন বেল টেলিফোন কোম্পানীর ল্যাবরেটরীতে কাজ করার সময় তাদের হর্ন এন্টেনার সাহায্যে এমন একটা দুর্বল রেডিও সিগন্যালের (পরম শূন্যমাত্রার উপরে 2.7 K ডিগ্রী) উপস্থিতি লক্ষ্য করেন যা চারিদিক থেকে সমান ভাবে ধরা পড়ে অর্থাৎ মহাবিশ্বের সর্বত্র তা সমান ভাবে বিদ্যমান। প্রথমে তারা এটাকে যান্ত্রিক ত্রুটি মনে করলেও উপর্যুপরি পরীক্ষাতে একই জিনিস ধরা পড়তে থাকে।
এর দীর্ঘদিন পরে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের সহায়ক গবেষণায় স্থির হয় যে বিগ ব্যাংগ থেকে ছড়িয়ে পড়া রেডিয়েশান যে এখনও মহাবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে বলে ধারণা করা হয়েছিল, নব আবিষ্কৃত সর্বত্র বিরাজমান 2.7K ডিগ্রী তাপমাত্রার এই দুর্বল রেডিও সিগন্যালই সেই বিকিরণ অবশেষ (Cosmic microwave background radiation)। বস্তুজগতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রাকে বলা হয় পরম শূন্যমাত্রা (Absolute zero degree), যার পরিমাণ মাইনাস ২৭৩.২ ডিগ্রী কেলভিন তাপমাত্রা। এই তাপমাত্রাতে সমস্ত পদার্থের মধ্যে বস্তুকণিকার স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে পড়ে এবং পদার্থ তাপমাত্রিক চির ভারসাম্যে পৌঁছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে পরম শূন্যমাত্রার উপরে ২.৭ ডিগ্রী তাপমাত্রা খুব কম মনে হলেও মহাবিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান এই উত্তাপের মোট শক্তির পরিমাণ বিশাল।
তাদের এই আবিষ্কারের ফলে বিশ্ব জগতের সৃষ্টি মুহূর্তের রহস্য সমাধানে এক গুরুত্বপূর্ণ 'ফসিল' পাওয়া সম্ভবপর হলো- যা একক বিন্দু থেকে বিস্ফোরিত ক্রমপ্রসারমান বিশ্বের ধারণাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। আর্নো পেনজিয়াস এবং রবার্ট উইলসন তাদের এই আকস্মিক, অথচ যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য চৌদ্দবছর পরে অর্থাৎ ১৯৭৮ সনে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন।
এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা আমাদের পৃথিবী থেকে যখন অতি দূরের নীহারিকাগুলোকে প্রত্যক্ষ করি তখন তাদের যে রূপ আমরা দেখি তা তাদের বর্তমান রূপ নয়, বরং কোটি কোটি বছর আগেকার আদি রূপ। আলোক রশ্মি তার অচিন্তনীয় দ্রুতগতিতে ভ্রমণ করলেও মহাবিশ্বের দূরতম বস্তু থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পড়তে যে সময় লাগে তার পরিমাণ বহু কোটি বছর বলে দৃশ্যমান বস্তুটির রূপ তার কোটি কোটি বছর আগেকার রূপ। মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশান আবিষ্কারের ফলে আমরা যে তথ্য পাচ্ছি তা মহাবিশ্বের উৎপত্তিকালীন সময়ের ৯৯.৯% কাছাকাছি সময়ের, কেননা এই রেডিয়েশানের উৎপত্তি হয়েছে বিগ ব্যাংগের ১০ লক্ষ বছরের মধ্যে। আর দূরবর্তী নীহারিকা আবিস্কারের মাধ্যমে আমরা দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে উৎপত্তি সময়ের ৭৫% কাছাকাছি যেতে সক্ষম।
বর্তমান কাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে দূরের বস্তু, যেমন কোয়াসার OH ৪৭১ অথবা ০১ ১৭২ আমাদের কাছ থেকে প্রায় ১৫ শত কোটি আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। এদের লোহিত বিচ্যুতির পরিমাণ যথাক্রমে ৩.৪ এবং ৩.৫৩ এবং এরা আলোকের প্রায় ৯০% গতিতে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সুতরাং আমরা যখন এগুলোকে দেখি তখন তা যে রূপে দেখতে পাই সেটা বিশ্ব সৃষ্টির সামান্য পরের মুহূর্তে তাদের রূপ- আলোকরশ্মি আমাদের কাছে পৌঁছুতে যত সময় লেগেছে, তাদের সে রূপও ততদিনের পুরোনো। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির টেলিস্কোপের মাধ্যমে এদের প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমাদেরকে শুধু ১৫ শত কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে ভ্রমণ করার সুযোগই দেয় না- আমাদেরকে ১৫ শত কোটি বছর অতীতে বিচরণ করার সুযোগও দেয়। পরবর্তী প্রজন্মের আরো উন্নত প্রযুক্তির টেলিস্কোপ নিশ্চয়ই আমাদেরকে সুযোগ দেবে আরো দূরবর্তী মহাজাগতিক পদার্থ আবিষ্কার করতে অর্থাৎ আমরা আরো অতীতে ভ্রমণ করার সুযোগ এর মাধ্যমে পাবো। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আমরা হয়তো দেখতে পাবো মহাবিশ্বের সৃষ্টি মুহূর্তের কাছাকাছি সময়ে তার আদিরূপ।




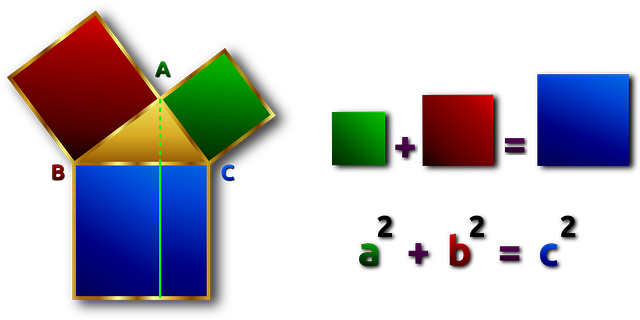








0 Comments